Despite that, Remember
Dr. Mali Mitra. Asst. Prof. In Music. Memari College. Memari. Burdwan.
Abstract:
Rabindranath a poet of the world. He is the Eternal Creator. Rabindranath Tagore is one such creator,
through whose creation we constantly reach in another dimension. Even in today’s
age, he is the immortal creator. A small portion of the vast range of his
contemporary art and literature has been discussed within limitations. That is –
transition from poetry created by the poet to song. There are many poems which
he composed as a poet. Later he expressed poetry through music. Through this
writing, on one hand, his literature and art are highlighted and on the other hand,
through discussion, I will talk about reaching songs from some of Tagore’s poems.
Word Index: Poet, Rabindranath, Poetry, Song, Literature, Art etc.
তবু মনে রেখো
ডঃ মলি মিত্র, সংগীত বিভাগ, মেমারি কলেজ, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
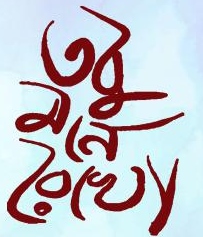
কালজয়ী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ । নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এলো তাদের বিচিত্র বিকাশের দিক বা পালা। এক একটি গান রচনা ও তাতে সুরযোজনা করে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে গানের শতদল ও সহস্র দল কমল রচনা করলেন। প্রতিটি গীত শৈলী বিভিন্ন ধারাবহন করে। রবীন্দ্রনাথকে গীত রচয়িতা এবং কবি হিসেবে যদি পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এই রচনা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কবি মন নিয়ে তিনি চোখে যা দেখেছেন তা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, আর গীতিকার হয়ে তিনি সংগীতের মাধ্যমে তাতে রং তুলি বুলিয়েছেন।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বললেন ভুল বলা হবে না। কারণ যে আত্মমগ্ন ধ্যান দৃষ্টি যে পরম জ্ঞান ও প্রতিভা যে দিব্য বৈরাগ্য আমাদের ভারতীয় ঋষিত্বের আদর্শকে মহীয়ান করে তাঁর প্রত্যেকটা গুণ ই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চিত। তবুও সবকিছুর উপরে, সবকিছুর মূলে রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কবি মানস কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা “জীবন- স্মৃতি” থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। “নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। ………………… কী বুঝিতাম, কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়। …………………… আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়েছে”[1].
শুধু ছেলেবেলায় নয় পরবর্তী সমগ্র জীবনেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কবি প্রকৃতিকে জয়যুক্ত করেছে। তাঁর সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবিদৃষ্টি। যে পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটে ছিল তা তাঁর জীবনের পরম পাওয়া। “ আমার বয়স তখন সাত – আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগনিয়ে শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের স্বাগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, ‘তোমাকে পদ্য লিখতে হইবে’ বলিয়া পসার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতি পদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন”[2]।
এই আবহাওয়াতেই কবির বড় হয়ে ওঠা। তাই একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তা হল এমন কোন বিষয় নেই যা রবীন্দ্রনাথের কলমের ছোঁয়ায় অন্যতম রূপ ধারণ করেনি। তাঁর ব্যাপ্তি ও বিশাল। এই বিশাল ব্যাপ্তির ভেতর থেকে কয়েকটি কবিতা থেকে গানকে খুঁজে নিয়ে আলোচনা প্রসারিত করব। তবে তা অবশ্যই স্বল্প পরিসরে। রবীন্দ্রনাথ আসলে হলেন কবি। তাঁকে সাহিত্যের ভাষায় বিশ্ব কবি বলা হয়। কবিতা ই মূখ্য।তবুও তিনি কবিতা থেকে গান রচনা করেছেন বহু একথা বলতে দ্বিধা নেই।
কবির জীবনে প্রথম থেকেই দেখা যায়, যেমন তিনি গান রচনা করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে কবিতারও জন্ম দিয়েছেন। কবিতা কবির প্রথম জীবনের কাব্য সূচনাকে সংগীত সাধনা বলেই তিনি চিহ্নিত করেছেন। ‘ছবি ও গান’ (১২৯০) থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে সংগীতের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় এক একটি তিনি সুরের অলংকারে অলংকৃত করেছেন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি “তবু” কবিতাটি কে নিয়ে।
কাব্য রূপ-
“ তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি, / সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে / হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি, / ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।“ কবিতা থেকে গান বাস্তব জীবনের চিন্তা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তারই প্রকাশ পায় এই কবিতাটির গীতরূপে। – “ তবু মনে রেখো, যদি দূরে যায় চলে। / যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে।। / যদি থাকি কাছাকাছি দেখিতে না পাও ছায়ার- মতন আছি না আছি – / তবু মনে রেখো। / যদি জল আসে আঁখিপাতে, / একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে, / একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ পাতে- / তবু মনে রেখো।“ এই গানটি কবি ২৬ বছর বয়সে রচনা করেন ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ‘তবু’। এই গানে তিনি বিপুল পরিবর্তন ঘটান। এই ২৬ বছর বয়সের কবি ছোট কবিতাটিকে যে গীতরূপ তিনি দিলেন, তা ভাষাকে ছাপিয়ে গেছে ভাবের প্রাচুর্যে। তিনি সকল বেড়াজালকে ভেঙে দিয়ে মুক্তি দিলেন বাণীকে সুরের রাজ্যে। এক অভূতপূর্ব উপলব্ধি। এই উপলব্ধি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে আজও সমমর্যাদায় আসীন।
কবিত্ব শক্তির দ্বারা তিনি যা কিছু অনুভব করেছেন তাকেই তিনি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতার মধ্যে। এই সৃষ্টিতে বিশ্ব কবির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম্য উপলব্ধি তাঁর সকল প্রকার সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর কবি মন আধ্যাত্মরসে দ্রবীভূত ছিল, আর এই প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় সংগীতের ক্ষেত্রে। ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “কে” কবিতাটিকে পরবর্তীকালে সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
কাব্য রূপ-
“ আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাস টুকুর মত ! / সে যে ছুঁয়ে গেল নিয়ে গেল রে, / ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত। / সে চলে গেল, বলে গেল না, / সে কোথায় গেল ফিরে এলো না, / সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,/ কি যেন খেয়ে গেল- / তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম -বনেতে। / সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে, চাঁদের আলোর দেশে গেছে।“ এই কবিতাটি যখন গানে রূপান্তরিত হয় তখন কিছু কিছু জায়গায় তিনি বদল ঘটিয়েছেন।
গীতরূপ-
“আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাস টুকুর মতো! / সে ছুয়ে গেল নয়ে গেল রে, / ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত । / সে চলে গেল, বলে গেল না, / সে কোথায় গেল ফিরে এলো না, :/ সে যেতে যেতে চেয়ে গেল, / কি যেন গেয়ে গেল – / তাই আপন মনে বসে আছি কুসুমবনেতে। সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে চাঁদের আলোর দেশে গেছে।“ এটি কবির ২২ বছরের রচনা। এই বয়সেই তাঁর অনুভূতি প্রকাশ ঘটে এই লেখনীর মধ্যে দিয়ে। এই কবিতাটি যখন গানে রূপান্তরিত হলো তখন কিছু কিছু জায়গায় তিনি বদল ঘটিয়েছেন কথার দিক থেকে। যেমন- কবিতায় আমরা দেখতে পাই ‘ঢেউয়ের মতো’ কিন্তু গানের স্থানে তিনি লিখলেন ‘ঢেউয়ের মতন’ আবার ‘কুসুম বনেতে’ তার আগে আমরা কবিতার জায়গায় ‘সে কুসুমবনেতে’ দেখি, এছাড়া কবিতায় দেখা যায় ‘মুদে এল’ গানের কথায় তিনি বললেন ‘মুদে এল রে’ ইত্যাদি । কথা যখন ব্যর্থ হয়, সাধারণ কথায় যখন কুলে ওঠে না, তখন কবিতা গান হয়ে ওঠে। আর সেই গান তখন মর্মস্পর্শী হয় । গানের মধ্যে সুরের আবেদন বেশি করে ফুটে ওঠে। তা অনির্বাচনের রূপ ধারণ করে। আসলে রবি ঠাকুরের কবিতার মধ্যে যে আত্মনিবেদনের আভাস পাওয়া যায় এবং গানের মধ্যে তিনি যে রসের সঞ্চার করেছেন, তাতে অপরূপকে হাজির করে তোলেন সুরলোকে। এই গানটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।
এই স্থানে রবি ঠাকুরের একটি উপলব্ধি প্রকাশ করি – “আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে – কথা ও সুর। কথা যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুর ও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে । একই কথা নানা সুরে, নানা অর্থ প্রকাশ করে”[3]।
এই এই বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আবেগ ও অনুভূতি থেকেই সংগীত ও কবিতার জন্ম , এবং আবেগ ও অনুভূতির উপর নির্ভর করেই সংগীত এবং কবিতার সৃষ্টি । কবি রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই নিজেকে বিলীন করে অসীম রহস্যকে ছুঁতে চেয়েছেন । কাউকে যেন তিনি ধরতে পেরেছেন, উপলব্ধি করেছেন আপন অনুভূতি দিয়ে। আসলে অনুভূতির ভাষা ছন্দবদ্ধ! কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রধান বলে মনে করি, আর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরের ভাষাই প্রাধান্য পায়। গানের সুর চিরকালই হৃদয়গ্রাহী। রবীন্দ্রনাথের আরো একটি কাব্যগ্রন্থ ‘সোনার তরী’। কাব্যগ্রন্থটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। এই গ্রন্থে ‘দুই পাখি’ নামের যে কবিতাটি আছে তা তিনি সংগীতে রূপান্তরিত করেন।
কাব্য রূপ-
“খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে / বনের পাখি ছিল বনে। / একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে, / কি ছিল বিধাতার মনে। / বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই, / বনেতে যাই দোঁহে মিলে, / খাঁচার পাখি বলে, বনের পাখি, আয় / খাঁচায় থাকি নিরিবিলে। / বনের পাখি বলে, না। / আমি শিকলে ধরা নাহি দিব। / খাঁচার পাখি বলে, হায়। / আমি কেমনে বনে বাহিরিব”। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব কবি তা এই কবিতায় প্রকাশ পায়। তিনি বিশ্বজগতের নানা বিচিত্র রূপ রসের সাথে এক হয়েই থাকতে চান। তাই ‘দুই পাখি’ এই কবিতায় তিনি শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধে উপনিষদের যে ধারণা আছে তাই ব্যক্ত করেছেন এর মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও এই রচনাটি সম্বন্ধে কবির ছোটবেলার কিছু মতামত আছে, যেভাবে তিনি বড় হয়েছেন তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনা। তিনি বলেছেন- “ বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ -মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গুন্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখানে দূরে, বাহির এখানে বাহিরেই”।[4]
গীতরূপ-
“ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, / বনের পাখি ছিল বনে। / একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে, / কি ছিল বিধাতার মনে। / বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই,/ বনেতে যাই দোঁহে মিলে, / খাঁচার পাখি বলে, বনের পাখি, আয় / খাঁচায় থাকি নিরিবিলে। / বনের পাখি বলে, না, / আমি শিকলে ধরা নাহি দিব। / খাঁচার পাখি বলে, হায়, / আমি কেমনে বনে বাহিরিব”। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিছু কবিতায় সুর দিয়েছেন। কখনো সমগ্র কবিতায়, আবার কখনো কিছু অংশে। তবে ‘দুই পাখি’ কবিতাটি কে সমগ্র অংশেই সুরের সংযোজন করেছেন মাত্র। সাধারণ ভাবে এই ‘খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে’- গানটি বাক-প্রধান, আর এটির সুরকে এবং কথাকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, কবিতায় সুরযুক্ত হয়েছে। সুর দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মধ্যে থেকে এমন কিছু রচনা বাছাই করে নিয়েছেন যা শুধুমাত্র ছন্দবদ্ধ নয়, যার মধ্যে ভাবের ব্যাপ্তি আছে। এই গানটি কে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, সম্পূর্ণ কবিতাটি সুরে গাওয়া হয়েছে মাত্র। এটি তাঁর ৩১ বছর বয়সের রচনা। কবি বলেছেন- “সংগীত কবিতার ভাই”।[5]
পরিশেষে বলতে পারি, কোন কবিতা থেকে কোন গানের সৃষ্টি তা পৃথকভাবে বলার বা বোঝাবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি – “অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবিতা ও সংগীতের আর কোন তফাৎ নাই — কেবল ইহা ভাব প্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাব প্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র”।[6]
কবিতা থেকে গানের সৃষ্টি হয়েছে, এই রকম উদাহরণ বহু পাওয়া যায়। তবে লেখনীর বেড়াজালে থেকে কবির আরও একটি অমর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করলাম। কবিতা ও গান এর কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলাম যার ভিতর থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কবির কথা বলে আলোচনার ইতি টানছি। কবি বলেছেন – “সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখিনা, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয় শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র। দেখা গেল সঙ্গীত ও কবিতা একশ্রেণীর”।[7]
তথ্যসূত্র
[1] জীবনস্মৃতি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পৃষ্ঠা – ৪৩৭ রবীন্দ্র রচনাবলী নয় খন্ড
[2] জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পৃষ্ঠা, ৪২৩ রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খন্ড
[3] সংগীত চিন্তা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -পৃষ্ঠা ১৮
[4] জীবনস্মৃতি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পৃষ্ঠা ৪১৫, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খন্ড
[5] সংগীত চিন্তা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -পৃষ্ঠা ২১
[6] সংগীত চিন্তা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পৃষ্ঠা ১৯
[7] সংগীত চিন্তা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পৃষ্ঠা ২০
সহায়ক গ্রন্থ
১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ – ছবি ও গান – বিশ্বভারতী।
২) দেবনাথ ধীরেন্দ্র- রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু – রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
৩) বসু অরুন কুমার – বাংলা কাব্য সংগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত – দেজ পাবলিশিং।
৪) বন্দ্যোপাধ্যায় কণিকা, বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র – রবীন্দ্রসংগীতঃ কাব্য ও সুর – করুণা প্রকাশনী।
৫) মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার – গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী – টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
৬) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ – সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান – শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা।